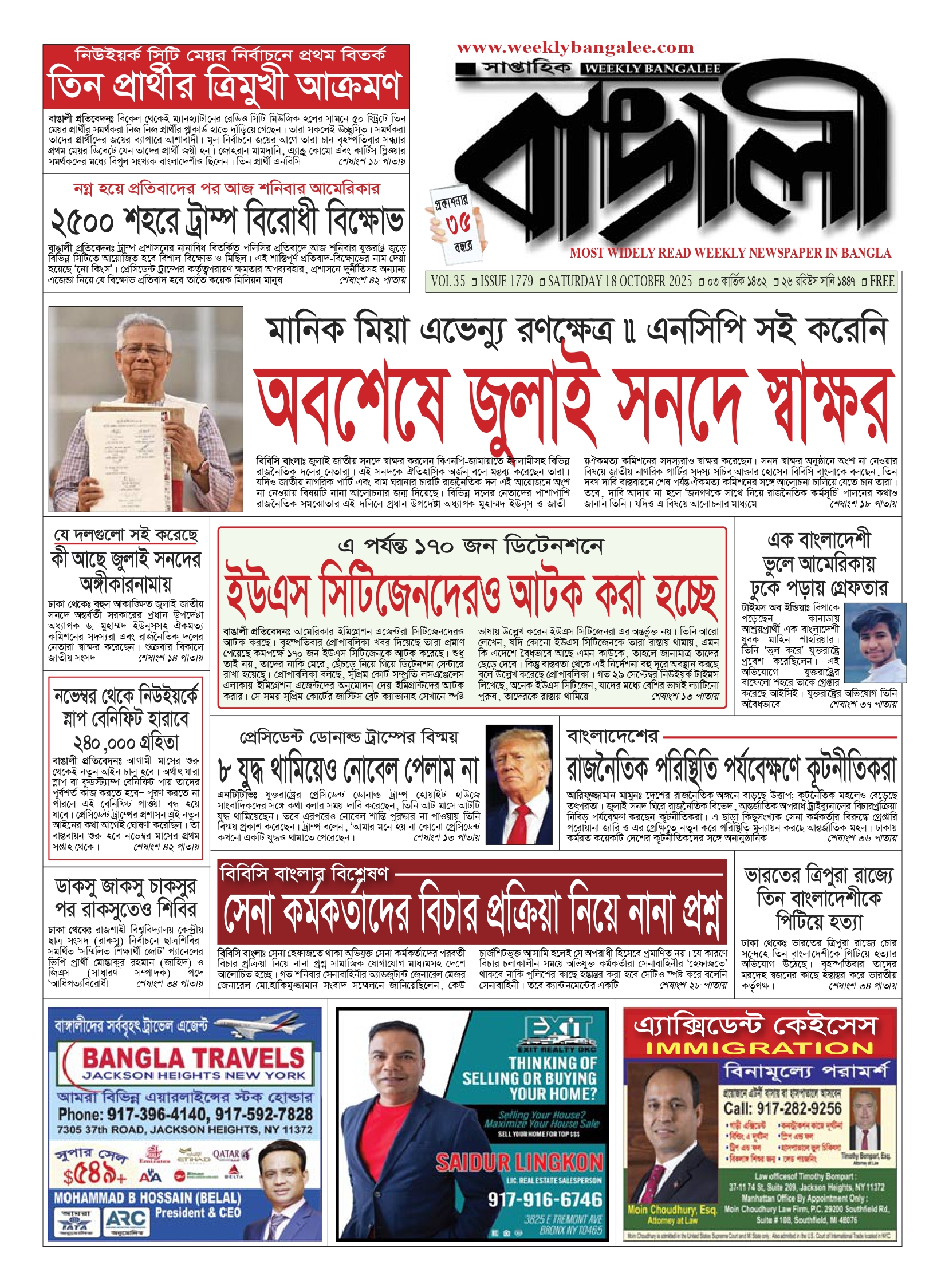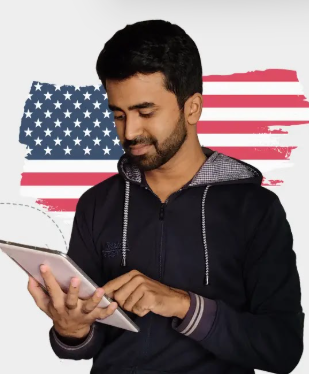জন্মদিনে একপাতা || আবেদীন কাদের

আত্মপরিচয়ের ইতিহাস এবং রাজনৈতিক প্রতাপ দ্বারা এর বিকৃতি!
একটি জাতির ইতিহাস বিষয়ে, বিশেষ করে রাষ্ট্র বিষয়ে ধ্রুপদী কয়েকটি তত্ত্ব সমাজবিজ্ঞানে খুব জরুরিভাবে শেখানো হয়। এই ইতিহাস সবচেয়ে নির্মোহভাবে লেখেন স্বাধীন ইতিহাসবিদরা। কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতা যদি কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণে থাকে তাহলে এই ইতিহাস নির্মাণে সেই ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নিয়ম, অন্বিষ্ট, রাজনৈতিক আদর্শ ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অনেক বেশি। এটা হয়তো সেই সব দেশে একটু অপেক্ষাকৃত কম হয় যেখানে আধুনিক রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া থিতিয়ে প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানগুলো শক্ত মাটির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর কারণ আইন ব্যবস্থা একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সেখানে অপেক্ষাকৃত স্বাধীন এবং যে কোন বিকৃতির বিরুদ্ধে আইন বা বিচারব্যবস্থা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে। কিন্তু যে সকল দেশে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানগুলো নড়বড়ে, সেখানে রাজনৈতিক দলগুলো এবং তাদের স্বার্থতাড়িত মহলগুলো ইতিহাস বিকৃতির চূড়ান্ত নজির রাখে তাদের স্বার্থেই, এটা বিশেষ করে ঘটে তৃতীয় বিশ্বের অগণতান্ত্রিক দেশগুলোতে। ফলে এসব দেশে রাজনীতি এবং সাংস্কৃতিক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়। উদাহরণ স্বরূপ আফ্রিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশের কথা উল্লেখ করা যায়।
আদিকাল থেকে আজ অবধি রাষ্ট্র পরিচালনার কয়েকটি ব্যবস্থা নিয়েই সমাজবিজ্ঞানীরা বেশি আলোচনা করেন, এবং সেই ব্যবস্থাগুলোর ব্যবচ্ছেদ করতেই তাত্ত্বিক বিষয়গুলো সামনে আসে। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য চষঁৎধষরংস, ঊষরঃরংস, গধৎীরংস ধহফ গধৎশবঃ— ষরনবৎধষরংস. কিন্তু এই সবগুলো ব্যবস্থার রাজনৈতিক ব্যবচ্ছেদেই আত্মপরিচয়ের ইতিহাস বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। যদি সেটিকে সঠিকভাবে বুঝতে হয় বা ব্যবচ্ছেদ করতে হয় তাহলে জানতে হবে আধুনিক রাষ্ট্র কীভাবে প্রতিষ্ঠা পায়, বিশেষ করে আধুনিক জাতি—রাষ্ট্র। জাতীয়তাবাদীরা, ভাষা—নির্ভর জাতীয়তাবাদী বা ধর্ম—নির্ভর জাতীয়তাবাদী বা অন্য কোন ধরনের জাতীয়তাবাদী, এমনকি তা নাৎসিদের উগ্র জাতীয়তাবাদীরাও, বিশ্বাস করে যে জাতি—রাষ্ট্রের সংজ্ঞা হওয়া উচিৎ যেভাবে ইতিহাস, সম্প্রদায় বা কমিউনিটি, ভাষা বা এথনিসিটি নির্ধারণ করে দেয়। আদিকালের কিছু রাজ—ভূখন্ডের অনেক সংখ্যক এথনিসিটিকে ধারণ করতে সক্ষম ছিল, যেমন হ্যাবসবার্গ বা অটোম্যান সাম্রাজ্যের রাজশাসন। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রগঠন কর্মকর্তা বা রাজনৈতিক এলিটরা সাধারণত যে— ভূখন্ড শাসন করে সেখানে বিবিধ এথনিক পরিচয়ের মানুষদের সম—চারিত্রিক বা একই এথনিক গোষ্ঠীর মানুষে পরিণত করে রূপান্তরের মাধ্যমে, অন্তত কমপক্ষে সেটা করতে চেষ্টা করে! এটাকে অনেকটা রূপান্তরিত ‘পরিচয়ের’ মধ্যেই আনার চেষ্টা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রায়ই এই রূপান্তরের প্রক্রিয়া চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। আর সেটা করে থাকে সংখ্যালঘু ধর্ম বা ভাষা—ভিত্তিক সম্প্রদায় বা অন্যান্য সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সম্প্রদায়গুলো। কিন্তু এই সমচারিত্রিকতা মাঝে মাঝে প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় অন্য বিকল্প সংখ্যালঘু ধর্ম, ভাষা, এথনিক গোষ্ঠী বা সংস্কৃতি দ্বারা। রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত জাতীয়তা হলে তাকেও প্রতিরোধ বা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয় অনেক সময়। আর কখনও কখনও সেই চ্যালেঞ্জ খুব তীব্র আকারেই হতে পারে। বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী উইল কিমলিকা সেটাকে বলেন এরকমভাবে, ‘অঃ ঢ়ৎবংবহঃ ঃযব ভধঃব ড়ভ বঃযহরপ ধহফ হধঃরড়হধষ মৎড়ঁঢ়ং ধৎড়ঁহফ ঃযব ড়িৎষফ রং রহ ঃযব যধহফং ড়ভ ীবহড়ঢ়যড়নরপ হধঃরড়হধষরংঃং, ৎবষরমরড়ঁং বীঃৎবসরংঃং ধহফ সরষরঃধৎু ফরপঃধঃড়ৎং. ওভ ষরনবৎধষরংস রং ঃড় যধাব পযধহপব ড়ভ ঃধশরহম যড়ষফ রহ ঃযবংব পড়ঁহঃৎরবং, রঃ সঁংঃ বীঢ়ষরপরঃষু ধফফৎবংং ঃযব হববফং ধহফ ধংঢ়রৎধঃরড়হং ড়ভ হধঃরড়হধষ সরহড়ৎরঃরবং.’
আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও এর ধ্রুপদী যে চারটি তত্ত্ব রয়েছে সেগুলো এই প্রতিরোধ সম্পর্কে তেমন কিছুই প্রায় বলে না। অথবা কেন একটা নির্দিষ্ট ভূখন্ডে জনগোষ্ঠীর জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থা সৃষ্টি করে তাও বলে না। আমরা জানি ‘নীচ থেকে ওপরে’ (ইড়ঃঃড়স ঁঢ়) ধরনে যে রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া চালু আছে, যেটা সন্ধান করে জাতীয়, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় বা ভাষাভিত্তিক জাতিকে রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা এবং নির্দিষ্ট ভূখন্ডে রাষ্ট্র নির্মাণ করে, সেটাকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বলেও ধরে নেয়।
অস্তিত্ব বা আত্মপরিচয়ের রাজনীতি কোন রাষ্ট্র এমনভাবে জোর দিয়ে দেখে যে এর জন্য অনেক সময় সেই রাষ্ট্রের নাগরিকগণ নিজে প্রাণ দিতে বা অন্যের প্রাণ সংহার করতে দ্বিধা করে না। ‘জাতি’ বলতে আমরা যা বুঝি তা সবসময় রাষ্ট্রের সীমানা দ্বারা চিহ্নিত থাকে না। যেমন বাংলাদেশ, পাঞ্জাব, বা আরও অনেক রাষ্ট্র রয়েছে যাতে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মত একই জাতিসত্তার মানুষ বাস করে। যেমন সুইজারল্যান্ড, বা অস্ট্রিয়া ও ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্র। কিন্তু সমস্যাটা বেশি ঘটে বহুজাতিক রাষ্ট্রে। যদিও জাতীয় বা রাষ্ট্রিক পরিচয় একমাত্র সমস্যা নয় জাতীয় পরিচয়ের ক্ষেত্রে। এগুলোর মধ্যে ধর্মীয় পরিচয়, ভূখন্ড, এথনিসিটি, লিঙ্গ পরিচয়ের সমস্যা, যৌনপ্রবণতা বা পরিচয়, এমনকি সামাজিক শ্রেণীসহ নানাবিধ সমস্যা। আজকের বিশ্বে রাষ্ট্র কয়েকটি সংঘর্ষপূর্ণ আত্মপরিচয়, বা প্রতিযোগী পরিচয়ের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে। কিছু কিছু রাষ্ট্র এসব সংঘাতপূর্ণ জাতীয় পরিচয় বা আত্মপরিচয়—সত্তা বিষয়ে বিবাদে জড়িয়ে দীর্ঘমেয়াদী সমস্যায় জর্জরিত হয়েছে। এদের মধ্যে ভাষা ও ধর্ম নিয়ে সংঘাত রয়েছে বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রে। কোন কোন রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ছায়ায় এসব সংঘাতকে কিছুটা প্রশমিত করতে সমর্থ হয়েছে, কিন্তু কিছু কিছু রাষ্ট্রে এই সংঘাত একেবারেই অগ্নিগর্ভের সৃষ্টি করেছে। এদের কেউ কেউ নিজেদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের দাবি তুলেছে, কেউ কেউ প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের আত্মপরিচয়কে একেবারেই স্বীকার করতে নারাজ। কিন্তু দিনের শেষে দেখা গেছে আত্মপরিচয় বা আত্মপরিচয়ের রাজনীতি সমাজে বড় ধরনের বিপত্তি ডেকে আনে। বাংলাদেশ তার বড় উদাহরণ। পাকিস্তান যদি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হত বা বাঙালিদের ভাষাভিত্তিক আত্মপরিচয়ের ইতিহাসকে মেনে নিত, তাহলে দেশটি হয়ত ভেঙে যেত না।
সংঘাতপূর্ণ আত্মপরিচয়ের বিবাদ রাজনীতিতে নতুন ঘটনা নয়, প্রাচীনকাল থেকেই এটার নজীর রয়েছে। ইহুদী সম্প্রদায় তাদের প্রতিবেশী সাম্রাজ্য থেকে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য বিবাদে লিপ্ত হয়েছিল অনেক আগে, তারপরের ইতিহাস, ইহুদীদের ইতিহাস সবার জানা। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে রোমান প্রজাতন্ত্রের ইতালীয় বন্ধুদেশগুলো যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল, যে যুদ্ধের মূল দাবি ছিল রোমান নাগরিকত্ব আদায় করা। কারণ তারা তখন ঝড়পরর স্ট্যাটাস নিয়ে জীবন চালাচ্ছিল, রোমান প্রজাতন্ত্রে মোট তিনটি বিভিন্ন স্ট্যাটাসভিত্তিক নাগরিক ছিল, ঝড়পরর তার মধ্যে একটি। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংরেজদের উপনিবেশগুলোতে জনগণকে যেমন ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দেয়ার দাবি উঠেছিল। ঝড়পরর স্ট্যাটাসের ধরন অনেকটা তার কাছাকাছি ছিল। কিন্তু অর্থনীতিসহ অন্যান্য বেশ কিছু সুযোগ নাগরিকত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। তাই এটাকে শুধু আত্মপরিচয়ের সংঘাত বলা যাবে না, এর সঙ্গে অন্যান্য সুযোগেরও সম্পর্ক ছিল। ধর্মীয় পরিচয়ের সংঘাত বা রাজনীতিও অনেক আগে থেকেই ছিল। আধুনিক রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়ার ইতিহাসের কয়েক শতাব্দী আগে থেকে ধর্মীয় সংঘাতের ইতিহাস ছিল। মানুষ ধর্মীয় পরিচয়কে প্রধান করে তার সঙ্গে রাজনীতিকে মিশিয়ে ভিন্ন সংঘাতের সৃষ্টি করেছে সেই সময়েও। যেমনটা দেখা মুসলিম ইতিহাসে আরব দেশগুলো থেকে স্পেন পর্যন্ত রাজ্য জয়ের ইতিহাস আসলে এক ধরনের নতুন ধর্মীয় আত্মপরিচয়ের ইতিহাস। পরবর্তী সময়ে খ্রিস্টীয় ধর্মীয় যুদ্ধগুলো মুসলিমদের ক্রুসেডের মাধ্যমে পরাস্ত করে নিজেদের আধিপত্য সৃষ্টি করে। এগুলো সবই ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক সংঘাতের ইতিহাস। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা বলে আমরা যা বুঝি তা আসলে ভাবনায় প্রথম আসে ১৬৪৮ সালের ওয়েস্টফেলিয়া চুক্তির সময় থেকে, যা আসলে করা হয়েছিল ইউরোপে ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্টদের মাঝের দীর্ঘ যুদ্ধের অবসান বা নিরসনের উদ্দেশে। এই চুক্তি ১৫৫৫ সালের ‘অগসবার্গ চুক্তি’র নীতিমালাকে অনুমোদন করে, যেখানে বলা হয় যে শাসক তার শাসিত ভূখন্ডে ধর্ম কী হবে তা নির্ধারণ করবে, কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত অবশ্য জুড়ে দেয় যে ১৬২৪ সালের আগে যে ধর্ম চালু ছিল তাও পুনর্বহাল করতে হবে। এই নীতিমালা সম্পর্কে এমন ধারণা তখন ছিল যে প্রতিটি রাষ্ট্র বা স্টেটের একটি ধর্ম থাকবে এবং সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে, যা অন্য রাষ্ট্রের ওপর প্রয়োগ করা যাবে যদি তাদের অন্য ধর্ম থাকে, বা নিজের ধর্মের নিরাপত্তা বিধান করা যাবে এই সার্বভৌম ক্ষমতা দিয়ে। কিন্তু ১৬৪৮ সালের পর রাজনীতিকগণ আত্মপরিচয়ভিত্তিক রাষ্ট্র নির্মাণের দাবি বেশ জোর দিয়ে উত্থাপন করেন এবং তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করেন, যা অনেক বেশি ছিল ইতিহাসবিদ বা ‘বুদ্ধিজীবীদের’ চাইতে। অন্যদিকে দেখা যায় ‘বুদ্ধিজীবীদের’ অবস্থান সবসময়ই পিচ্ছিল, তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্মের প্রতি তাদের আনুগত্য দেখান। মধ্যযুগের ইউরোপের, বিশেষ করে সেন্ট্রাল ইউরোপের ‘বুদ্ধিজীবীগণ’ খুব বেশি একটা বিশ্বাসযোগ্য মানুষ ছিলেন না। যারা, বা যেসব দল উপদল ‘জাতীয় আত্মপরিচয়’ বিষয়ক রাজনৈতিক এজেন্ডা এগিয়ে নিতে চাইত, তারা নিজেদেরকে এই বিষয়টি নিয়ে ভাববার জন্য গুরুত্বপূর্ণও মনে করত, কারণ তাদের ধারণা ছিল যে রাজনীতিতে এই আত্মপরিচয় বিশেষ গুরুত্ব বহন করে, অন্তত এথনিক ও জাতীয় রাজনীতিতে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ না হলেও। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পন্ডিতরা মনে করতেন যে আত্মপরিচয়ের রাজনীতি বা আইডেনটিটি পলিটিক্স অবশ্যই রাজনীতির সামাজিকভাবে কষ্টকল্পিত বা কন্সট্র্যাক্টেড ও পরিবর্তনশীল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে অধিক গুরুত্ব দেয়, বা দিতে বাধ্য। কারণ রাজনীতির অন্তর্গত বৈশিষ্ট্যের মাঝে এক ধরনের পরিবর্তনশীলতা রয়েছে যাকে রোধ করা সহজ নয়, তাই একে ধ্রুব না ভাবাই শ্রেয়। যদিও এর ব্যতিক্রম রয়েছে। সেমুয়েল হান্টিংটন তাঁর বিখ্যাত বই ঈষধংয ড়ভ ঈরারষরুধঃরড়হং—এ দেখিয়েছেন যে আইডেনটিটি বা আত্মপরিচয় অতি প্রাচীন এবং এটা প্রাকৃতিক, এটিকে পরিবর্তনের সুযোগ নেই। কিন্তু কোনো কোনো রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ঠিক এর উল্টো মত দিয়েছেন। বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী রবার্ট কাপলান তাঁর বইতে উল্টো কথা লিখেছেন, তিনি জানিয়েছেন যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনকে এই বলে সমাজবিজ্ঞানীরা রাজী করিয়েছিলেন যুগোস্লাভিয়াতে আক্রমণ করতে যে সেখানে বহু প্রাচীন আন্ত—এথনিক ঘৃণা এমন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে যা মানবতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই মার্কিন হস্তক্ষেপ জরুরি। কারণ জাতীয় পরিচয় কোনো ধ্রুব কিছু নয়, তা কালের বিবর্তনে বদলে যেতে বাধ্য হয় অন্যান্য রাজনৈতিক বাস্তবতার কারণে! যাহোক, পন্ডিতদের কেউ কেউ মনে করেন, আত্মপরিচয় বা আইডেনটিটি সময়ের বিবর্তনে বদলায় বা ‘গড়ে’ ওঠে। তাই আত্মপরিচয়ের ইতিহাসে দুটো সংজ্ঞাকেই মান্য করা হয়। কিন্তু রাজনৈতিক সংস্কৃতির সাথে এর সম্পর্ককে অস্বীকার করা কঠিন। খ্রিস্ট ধর্ম প্রথমে অন্য ধর্ম বা নাস্তিকদের অস্বীকার করত, মৌলবাদীরা আজও উদারনীতিক জীবনযাপনকে অস্বীকার করে বা অনুমোদন করে না, আবহাওয়া—প্রেমিকরা আজও ভোগবাদী শিল্পজগতকে বিশ্বের জন্য ক্ষতিকর মনে করে, রেডিকেল মুসলিমরা পশ্চিমা গণতান্ত্রিক বা উদারনীতিকে ঘৃণা করে, জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকরা আন্তর্জাতিকতাবাদকে বর্জন করে, ঠিক তেমনি বিচ্ছিন্নতাবাদীরা জাতীয়তাবাদী একরোখা নীতিকে অস্বীকার করে, তারা নিজেদের আত্মপরিচয়ের সংজ্ঞা ভিন্নভাবে দেয়, এবং নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান থেকে নিজেদের ভাগ্য গড়ে নিতে চায়। সেখানেই রাষ্ট্রের সংজ্ঞা এবং আত্মপরিচয়ের সংজ্ঞা ভিন্নভাবে রূপ নেয়!
রাষ্ট্র এই আইডেনটিটি পলিটিক্স বা আত্মপরিচয়ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা কীভাবে গ্রহণ করে। এর সঙ্গে দ্বন্দ্বময় নাকি অবস্থা বিশেষে পরিবর্তনীয়। এই প্রশ্নের মীমাংসা কঠিন, কারণ রাষ্ট্রকে দুদিকেই হেলতে দেখা যায়। রাষ্ট্র প্রথমে বিচার্য মনে করে ‘আত্মপরিচয়’ আসলে কী এবং কার আত্মপরিচয়! রাষ্ট্রে বা কোন সমাজে যে আত্মপরিচয়ের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সেই জনসমষ্টির সংখ্যা এবং প্রতাপের প্রকৃতিই বা কী রকম, তা বিশেষভাবে গুরুত্ব বহন করে! তাই আত্মপরিচয়ের উৎস কেবল অর্থনৈতিক স্বার্থই নয়। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ক্লাসিক্যাল প্লুরালিস্ট থিওরি অনুযায়ী অর্থনৈতিক স্বার্থ নেগোসিয়েবল হিসেবে ধরা হত, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ধারা অনুযায়ী। কারণ অর্থনৈতিক স্বার্থ মেটাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক ‘পুরস্কার’ প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে কাজ করে। আর খুব সহজেই প্রতিযোগী রাজনৈতিক শক্তিগুলোকে এই ‘পুরস্কার’ দিয়ে বশে আনা সম্ভব। পুঁজি এই ‘পুরস্কার’ উদ্ভাবন বা প্রদানে সাহায্য করে থাকে। তাই আংশিক হলেও পুঁজি রাষ্ট্রব্যবস্থায় শেকলের ভূমিকায় কাজ করে। এভাবে ইধৎমধরহবফ ঝড়ষঁঃরড়হ বা রাজনৈতিক সমাধানে আসতে প্রতিযোগী শক্তিগুলোকে পুঁজি সাহায্য করে। কিন্তু যেহেতু আইডেনটিটি কোনো ধ্রুব নয়, তাই তাকেও দিনের শেষে পরিবর্তনশীল বা নেগোসিয়েবল অবস্থায় রূপ নিতে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়ার কয়েকটি দেশে আইডেনটিটি পলিটিক্স বা আত্মপরিচয়ের ইতিহাস এভাবেই তার রূপ পরিবর্তন করেছে। প্লুরালিস্ট রাজনীতিকরা তাই ভেবেছেন গোড়ায়, কিন্তু এর অন্যথাও ঘটেছে। কারণ তারা ভেবেছে সব রাজনৈতিক ব্যাধির নিরাময় পুঁজির বিকাশ, কিন্তু আধুনিকায়ন বা পুঁজির বিকাশ আইডেনটিটি পলিটিক্স বা এথনিক সংঘাতকে বিলোপ করতে সমর্থ হয়নি। সাময়িকভাবে তা দমিত পর্যায়ে থাকে বা ছিল, কিন্তু মাঝে মাঝেই তা রূপ বদলিয়ে সামনে আসে। পুঁজিই শেষ নিরাময় নয়। আইডেনটিটি পলিটিক্স মার্কসবাদ ও পুঁজি দুটোকেই কখনও কখনও চ্যালেঞ্জ করে।
আইডেনটিটি পলিটিক্স অধিকাংশ সময় সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়। কিন্তু আত্মপরিচয় বা আইডেনটিটি রাজনীতি সংস্কৃতির সঙ্গেই একমাত্র জড়িত বা সংস্কৃতিই এর উৎস নয়। যেমন উত্তর আয়ারল্যান্ডে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিন্দুমাত্র পার্থক্য নেই, কিন্তু রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব প্রায় অমীমাংসিতই রয়ে যায় বহুদিন। সেখানে প্রটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিকরা দেখতে একই রকম, একই ভাষায় কথা বলে, একই পোশাক পরে, একই রকম রক্ষণশীল জীবনের ধারা দ্বারা অভ্যস্ত, একই রকম পানীয় পান করে, অস্বাস্থ্যকর খাবার খায় দুই সম্প্রদায়ই, কিন্তু তাদের আইডেনটিটি দুরকমভাবে তারা বিচার করে এবং আত্মপরিচয়ের রাজনীতিতে বিপুল সহিংসতা রয়েছে। ভূতপূর্ব ইয়োগোস্লাভিয়াতে সাংস্কৃতিক পার্থক্য প্রায় নেই বললেই চলে, কিন্তু আইডেনটিটি পলিটিক্স দেশটিকে প্রায় রক্তাক্ত করে রেখেছে অনেকদিন!
আইডেনটিটি পলিটিক্স বা আত্মপরিচয়ের রাজনীতি আক্ষরিক অর্থে প্লুরালিস্টিক, অর্থাৎ একাধিক পরিচয়ের এথনিক জনগোষ্ঠীর সমাজে এই রাজনীতি বর্তমান। এটা তখনও সত্য থাকে যখন একটি ফ্যাসিবাদী দলও রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে, হিংসার রাজনীতির সাহায্যে এক জাতীয়তার রাজনীতি সমাজের ওপর চাপিয়ে দিতে উদ্যত হয়। সেখানে একটি পরিচয়ের মানুষ প্রতাপের সংগে বলে অন্য পরিচয়ের বা এথনিক গোষ্ঠীর মানুষকে নিষ্পেষণ করে এবং দমিয়ে রাখার চেষ্টা করে। সে কারণেই দেখা গেছে রেডিকেল জাতীয়তাবাদী সার্ব, ক্রোয়েশিয়ান, বসনিয়ান, আলবেনিয়ান ও ইয়োগোস্লাভ সকল পরিচয়ের মানুষকেই প্রত্যাখ্যাত হতে হয় সার্ব রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ার ক্ষেত্রে। এর দায় ও পরিণাম ছিল ভয়াবহ। সার্ব নেতা স্লোবদান মিলসোভিচ, যিনি যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচারের সন্মুখীন হতে বাধ্য হয়েছিলেন, তার একটি কথা গুরুত্ব বহন করে, ‘জাতীয় পরিচয় হারানোর মূল্য কত ভয়ঙ্কর তা হারিয়ে যাওয়া পরিচয়ের জাতিটি খুব কমই অনুধাবন করতে পারে।’
প্লুরালিজম একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসেবে বহুধা বিভক্ত পরিচয়ের মানুষকে একোমোডেট করে, একই রাজনৈতিক ছাতার নীচে সম—অধিকার বণ্টন করে কিছুটা স্বস্তিতে রাখতেও সমর্থ হয়, কিন্তু এটা করতে হলে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিভিন্ন দেশে যে নির্দিষ্ট কোনো গোষ্ঠীর স্বার্থকে বেশি গুরুত্ব দেয়ার রেয়াজ গড়ে ওঠে তা বন্ধ করা জরুরি, কিন্তু পুঁজির নিজের অন্তর্গত চরিত্রে এর বিপরীত প্রকৃতি বিদ্যমান। পুঁজি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকেই অর্থনৈতিক বা অন্যান্য রাজনৈতিক স্বার্থ দিতে বদ্ধপরিকর। তাই আধুনিক সমাজে বিভিন্ন এথনিক বা আত্মপরিচয়ের গোষ্ঠীর সহিংসতার রাজনীতিকে পরিহার করা দুরুহ। সমাজও পুঁজির এই দোধারি তলোয়ারের নীচে পিষ্ট। একদিকে পুঁজির বিকাশ ও শক্তি সঞ্চয়, অন্যদিকে তা থেকে উদ্ভূত বহুজাতিক গোষ্ঠীর স্বার্থসংশ্লিষ্ট সমস্যার জায়মান প্রবৃদ্ধি! এই দুয়ের সামাল দিয়ে শ্রেয়তর সমাজগঠন সত্যিই দুরুহ, পুঁজির প্রতাপকে রুখে দিয়ে!